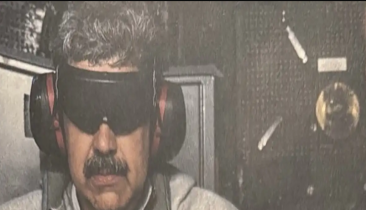রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী : আদি ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা
নুসরাত জাহান
প্রকাশিত: ২২:০১, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫; আপডেট: ০০:৫১, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

রাখাইন রাজ্যে ক্রমেই নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে আরাকান আর্মি (এএ)। ছবি : স্টিমসনডটওআরজি।
বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতিতে দিনদিনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে রোহিঙ্গা ইস্যু। এ রোহিঙ্গা কারা, কেন তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে, কতোজন রোহিঙ্গা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, শরণার্থী শিবিরের পরিস্থিতি, এ শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং জাতিসংঘের প্রস্তাবিত 'মানবিক করিডোর' - এসব বিষয় নিয়েই বিস্তারিত এ আলোচনা। আজ প্রকাশিত হলো এর চতুর্থ ও শেষ কিস্তি।
রাখাইন রাজ্যে আবারও অস্থিতিশীলতা ও রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থা
আরাকান রাজ্যে সম্প্রতি আরাকান আর্মি (এএ) ও আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) - এর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা ওই রাজ্যে অস্থিতিশীলতা আবারও বাড়িয়ে দিয়েছে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ ২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত নতুন করে আরও প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় (আরআরআরসি) সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
নতুন আসা এ রোহিঙ্গারা নাফ নদীর বিভিন্ন পয়েন্টসহ টেকনাফ, সেন্টমার্টিন ঘুরে শাহপরীর দ্বীপসহ বিভিন্ন জায়গা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকার শুরুতেই আর কোনো রোহিঙ্গাকে আশ্রয় না দেওয়ার নীতিগত অবস্থান ঘোষণা করলেও রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ থামানো যায়নি।
এদিকে, ২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর থেকে আরাকান আর্মি সমমনা আরও দুটি বিদ্রোহী দলের সঙ্গে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে জোট গঠন করে মিয়ানমারের জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত হামলা শুরু করে। বছরজুড়ে সেনাবাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলার মধ্য দিয়ে রাখাইন রাজ্য নিজেদের দখলে নেয় আরাকান আর্মি। ২০২৪ সালেও উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলমান থাকায় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে, ২০২৩ সালে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য নেওয়া পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রমও থেমে যায়। এ অবস্থায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রশ্নে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমার সরকারের পাশাপাশি আরাকান আর্মির সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকার।
কিন্তু, এখানে উল্লেখ করার বিষয় হলো, মিয়ানমারের জান্তা সরকার শেষ পর্যন্ত যদিও ‘রোহিঙ্গা’ শব্দটি মেনে নিয়েছে, কিন্তু, এ শব্দটি মানতে বরাবরের মতোই অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে রাখাইনের আরাকান আর্মি । গত ১৩ এপ্রিল এ দলটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে ৭টি শর্ত দেওয়া হয়, যাতে তারা রোহিঙ্গাদের ‘বাংলাদেশের (চট্টগ্রামের) মুসলিম শরণার্থী’ হিসেবে অভিহিত করে। এ অবস্থায়, বিপুল সংখ্যক এ রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রত্যাবাসনের বিষয়টির মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

'মানবিক করিডোর' ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গ
জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত ত্রাণ সংস্থা 'স্পেশাল অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল ফর মিয়ানমার' ২০২৪ সালের ১৯ আগস্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে রাখাইন রাজ্যের জন্য একটি মানবিক করিডোর চালু করতে এবং রাষ্ট্রের জাতিগত ও ধর্মীয় সব সম্প্রদায়ের কাছে ত্রাণ সরবরাহের অনুমতি দিতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য আরাকান আর্মির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেসও রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ে সব অংশীজনকে নিয়ে সংকটের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একটি র্কাযকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
এ লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মার্চে বাংলাদেশ সফরে এসে জাতিসংঘ মহাসচিব মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ত্রাণ সহায়তার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে বাংলাদেশকে অনুরোধ করেন।
তবে, বাংলাদেশে 'মানবিক করিডোর' বিষয়টি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, 'মানবিক করিডোর' এমন এক ব্যবস্থা যেখানে জরুরি প্রয়োজনে দুর্যোগপূর্ণ বা যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি অঞ্চল থেকে নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। ফলে, 'মানবিক করিডোর' সুবিধার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চল তথা কক্সবাজারের সীমান্তকে রোঙ্গিাদের জন্য নিরাপদ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা হবে কি না, এ প্রশ্নে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে, রাখাইনে ত্রাণ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হলে সীমান্তে মাদক ও অস্ত্র চোরাকারবারি এবং মানবপাচারের মতো অপরাধ বেড়ে যাওয়া এমনকি দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়।
এ অবস্থায়, 'মানবিক করিডোর' নয়, বরং বাংলাদেশ শুধু মিয়ানমার সীমান্তে ত্রাণ পৌঁছানোর কাজটি করবে বলে সংবাদমাধ্যমকে জানান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। এ ক্ষেত্রে, জাতিসংঘ তাদের নিজস্ব সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে রাখাইন অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছে দেবে এবং ত্রাণ ওপারে নিয়ে যাওয়া ও এ সংক্রান্ত নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ জাতিসংঘের হাতে থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
তবে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় রোহিঙ্গাদের তৃতীয় কোনো দেশে পুনর্বাসনের জন্য জাতিসংঘের কাছে সহায়তা চান। একইসঙ্গে, জাতিসংঘ সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনেরও প্রস্তাব দেওয়া হয়। পরে জাতিসংঘে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীতও হয়। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সচিবালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

এ অবস্থায়, সম্মেলন-পরবর্তী সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে হয়তো সুস্পষ্ট হতে পারে কক্সবাজারে অবস্থানরত বিশালসংখ্যক এ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাব।
তবে, রোহিঙ্গাদের সুষ্ঠু ও সফলভাবে প্রত্যাবাসনই যে এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়, এ বিষয়টি বাংলাদেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও একবাক্যে স্বীকার করে থাকে। বাংলাদেশ সফরকালে জাতিসংঘ মহাসচিবও এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় প্রসঙ্গে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যথাযথভাবে নিজ দেশে প্রত্যাবাসনের ওপরই জোর দিয়েছেন।
কিন্তু, বিষয়টি সবাই অনুধাবন করলেও এটি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো- বর্তমানে রাখাইনে চলমান সংঘাতময় পরিস্থিতি। মিয়ানমার জান্তা সরকার থেকে ক্রমাগতভাবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বছরের পর বছর নানা শর্ত দিয়ে বিষয়টি দীর্ঘ ও জটিল করা হয়েছে। আর, বর্তমানে ওই অঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করায় প্রত্যাবাসনের কাজটি একপ্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যেই পড়ে গেছে।
তবে, কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করা হয়। এসব তথ্যের মাধ্যমে সরকার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়াটি কোন পর্যায়ে রয়েছে, সে বিষয়ে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে।
এ ক্ষেত্রে, জান্তা সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান একটি শর্ত ছিলো বাংলাদেশের শিবিরে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের তথ্য যাচাই-বাছাই করা। অর্থাৎ, কারা দেশটিতে ফেরত যেতে পারবে, সে বিষয়টি নির্ধারণ করতে মিয়ানমার সরকার থেকে বাংলাদেশের কাছে তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত কয়েক দফায় মোট ৮ লাখ রোহিঙ্গার তথ্য মিয়ানমার সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমার সরকারের বিশেষ দূতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এতে ওই ৮ লাখ রোহিঙ্গার মধ্যে আড়াই লাখের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে বলে জানানো হয়। একইসঙ্গে, এর মধ্যে ১ লাখ ৮০ হাজার জনকে প্রত্যাবাসনযোগ্য বলে মিয়ানমার সরকার থেকে নিশ্চিত করা হয়। বাকি ৭০ হাজার শরণার্থীর তথ্যে থাকা ভুল-ক্রটি শিগগিরই বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বসে সংশোধন করা হবে।

এর মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের প্রাথমিক একটি প্রক্রিয়া শুরু হলেও বর্তমানে রাখাইন অঞ্চল আরাকান আর্মির দখলে থাকায় জান্তা সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রক্রিয়ার কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবশ্য, প্রক্রিয়া চলমান রাখতে এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আরাকান আর্মির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্র জানায়। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার দায়ভার মিয়ানমার সরকারের ওপর বর্তায় বলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। একইসঙ্গে, মিয়ানমার সরকারকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
তবে, আরাকান আর্মির পক্ষ থেকে রাখাইনের পরিস্থিতি অনুকূল হলে প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ সরকার।
পরিশেষ
রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ও মানবিক করিডোরের মতো বিষয়গুলো এ সংকট সমাধানে বর্তমানে সামনে চলে আসছে। এসবের কোনোটি বাস্তবায়িত হওয়া বা হলেও রোহিঙ্গাদের অবস্থার উন্নতির বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে সময় সাপেক্ষ একটি বিষয়। তবে, বাস্তবতা হচ্ছে - ক্ষুদ্র এ জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা বহু প্রজন্ম ধরে নিজ দেশে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। ফলে, সাংবাদিক ও লেখক ফ্রান্সিস ওয়েড মনে করেন- যতো উদ্যোগই নেওয়া হোক না কেন, একটি গোষ্ঠী ও এর সংস্কৃতি রক্ষা ও একে সংরক্ষণ করা, এমনকি রোহিঙ্গাদের 'মানুষ' হিসেবে মেনে না নেওয়া পর্যন্ত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতির উন্নতি কখনো সম্ভব নয়।
তথ্যসূত্র
https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_refugees_in_Bangladesh,
https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis,
বিবিসি বাংলা,
বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা,
প্রথম আলো ও বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম।